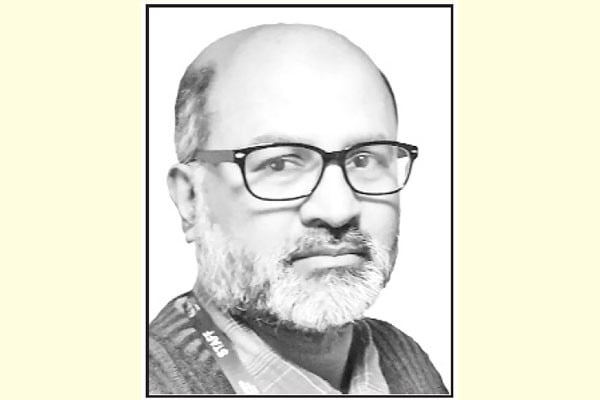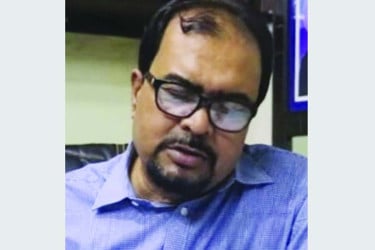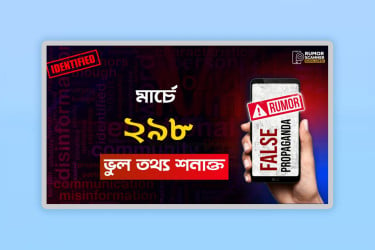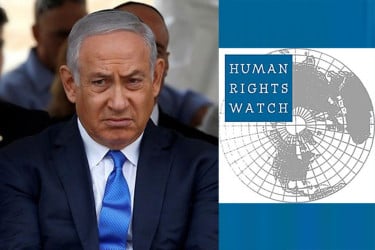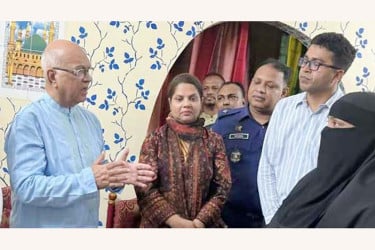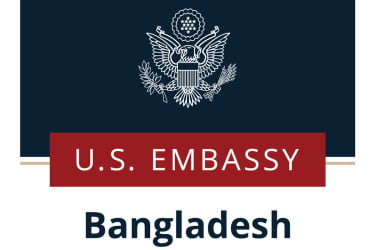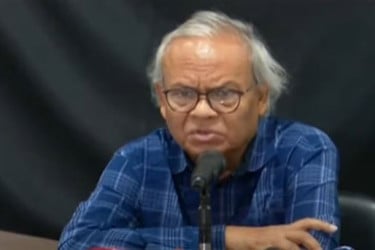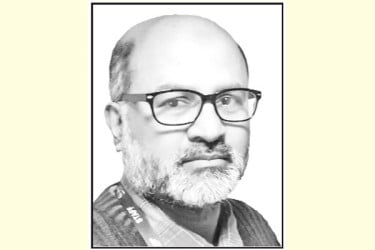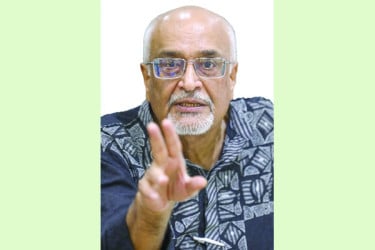বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ইত্যাদি দাবির তোড়ে ভিতরে ভিতরে নতুন নিয়োগ একদম বেখবরে। সরকারি-বেসরকারি উভয় সেক্টরেই নতুন নিয়োগে বেদম খরা। তার ওপর বেসরকারি সেক্টরে চাকরিচ্যুতি। যৌক্তিক-অযৌক্তিক মিলিয়ে গত ছয় মাসে শ দেড়েক আন্দোলনে সাধারণ মানুষের নসিবে জুটেছে ভোগান্তি। আর ব্যবসা-বিনিয়োগে অবিরাম খরার টান। একটু স্বস্তি কেবল রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে। অন্তর্র্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে রিজার্ভ প্রতি মাসে গড়ে এক বিলিয়ন ডলার করে কমছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম সাত মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৫৯৬ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ২৩ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।
সাত মাসে রপ্তানি হয়েছে মোট ২ হাজার ৮৯৭ কোটি ডলারের পণ্য, আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে তা প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। ডিসেম্বর শেষে রিজার্ভ বেড়ে ২১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। সেখানেও এখন ডেভিল ঘুরছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, জুলাই-আগস্টে সরকার পতনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শক্তির অনৈক্য, অন্তর্র্বর্তী সরকারের কাজে ধীরগতি রেমিট্যান্সের সুপ্রবাহে বাধার শঙ্কা তৈরি করছে। পতিত-বিতাড়িত দলটির দেশত্যাগী নেতা ও তাদের একাধিক উইং রেমিট্যান্সের প্রবাহে ছেদ ফেলার অপতৎপরতায় নেমেছে। এরই মধ্যে তাদের প্রবাসী সংগঠনগুলো পরিকল্পনামাফিক বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।
পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে অন্তর্বর্তী সরকার একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছে সত্য। ছাত্র-গণ আন্দোলনে সরকার পতনের পর রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে স্বস্তি এলেও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর করেছে নিরাপত্তাহীনতা। অথচ তারা অপেক্ষমাণ ছিল একটি স্বস্তিদায়ক কর্মপরিস্থিতির। বাস্তবতাটা হয়ে গেল বিপরীত। দুঃখজনকভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অস্থিরতা। আইনশৃঙ্খলার উন্নতির লক্ষণ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে আরও অবনতি ঘটেছে। অবস্থার উন্নতির আশায় সারা দেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু করেছে সরকার। তা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটালে অর্থনৈতিক সেক্টরে স্বস্তি যোগ করবে। নইলে ব্যবসা-বিনিয়োগে চলমান মরা কটালকে আরও তেজী করবে। প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে ব্যবসায়ী মহলকে। ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের হার, ডলার সংকট, এলসি জটিলতায় কাঁচামাল আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি গ্যাস ও জ্বালানিসংকটের কারণে কমছে উৎপাদন। অনেক কারখানা ঠিকমতো বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারছে না। বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কমতে কমতে এখন প্রায় তলানিতে।
গত ডিসেম্বরে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৮ শতাংশে, যা এখন পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৫০ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি ঋণ ছিল ৪ লাখ ১৫ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। তারল্য ব্যবস্থাপনায় ভয়াবহ সংকট, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, টাকার অবমূল্যায়ন, বিনিয়োগ মন্দাসহ নানা কারণে বেসরকারি বিনিয়োগে এ ভাটার টানে জোয়ার আনার মতো কোনো রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। পতিত সরকারের শেষ দিক থেকেই পুঁজির টান পড়েছে ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের কারও কারও। নতুন বিনিয়োগের সামর্থ্য হারিয়ে যায় অনেকের। সামর্থ্যবানরা বিনিয়োগের সুরক্ষার কোনো নিশ্চয়তা মিলছে না। মাঝেমধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের খবর এলেও বাস্তবে লক্ষণ নেই। দেশিবিদেশি বিনিয়োগ কমতে থাকায় কর্মসংস্থানে বুলডোজার পড়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এরই মধ্যে বেশ কিছু মিল-ফ্যাক্টরিতে চাকরি খোয়া গেছে অনেকের। চাকরি হারানোর শনি ঘুরছে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে। জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বেকারত্বের মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে তা ছিল ৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।
রপ্তানিমুখী শিল্পসহ অন্যান্য কারখানার উৎপাদন সংকট অব্যাহত থাকলে কর্মসংস্থানের এ চিত্র আরও ভয়াবহ হবে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহের মতো প্রধান শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গ্যাসসংকটের কারণে পোশাক খাতের উৎপাদন প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে। দেশে ১ হাজার ৮০০টি টেক্সটাইল মিলের মধ্যে ৭০০টি স্পিনিং মিল। গ্যাসসংকটের কারণে ৫০ শতাংশ মিল বন্ধ হয়ে গেছে। এ সুযোগে ভারত থেকে বৈধ-অবৈধভাবে সুতা আমদানি হচ্ছে। এ মিলগুলো পুরোদমে চালু থাকলে আরও ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতো। সিরামিকশিল্প সম্পূর্ণভাবে গ্যাসনির্ভর। সেখানেও চরম হাহাকার।
বেশির ভাগ কারখানায় উৎপাদনক্ষমতা অর্ধেকে নেমে এসেছে। গ্যাস না পেয়ে কোনো কোনো কারখানায় কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। এর মাঝে জ্বালানি তেলের দাম আবার বাড়িয়ে দেওয়ায় আগুনে ঘি পড়ার অবস্থা হয়েছে। দেশে যখন নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন, উদ্বেগজনক হারে কমছে বিদেশি বিনিয়োগ, বেসরকারি কলকারখানায় চলছে ছাঁটাই, সরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থানেরও সুসংবাদ নেই, এ রকম সময়ে টোকা পড়ল জ্বালানি তেলের দামে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নেমেছে গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এ খরা আরও বেগবান হয়েছে দেশে পট পরিবর্তনের পর থেকে। এ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ১০ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে প্রায় ৭১ শতাংশ, যার প্রভাবে বেপজার শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পেও বিনিয়োগ কমেছে ২৩ শতাংশ। বিদেশি বিনিয়োগের এ নমুনায় হাত গুটিয়ে বসে আছেন দেশীয় উদ্যোক্তারাও। এ দুরবস্থার জন্য এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল নীতি, উচ্চ সুদহার ও গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা। তার ওপর রাজনৈতিক সরকার না থাকাও একটি মোটাদাগের ঘটনা। দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্বর্তী সরকার কতটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে, এ প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠেছে।
ছোট, বড়, মাঝারি কোনো প্রভেদ নেই। সব শিল্পকারখানাতেই হাহাকার। একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারখানা। এতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে নেমে এসেছে কর্মচ্যুতিও। একদিকে মালিকরা ঋণগ্রস্ত, আরেকদিকে কর্মীদের হাহাকার, বেতন-ভাতা অনিয়মিত। সেই সঙ্গে চলছে ছাঁটাইও। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় তারা ক্রেতাদের অর্ডারের পণ্য দিতে পারছেন না। এর পরও শেষ চেষ্টা হিসেবে কিছু কিছু ফ্যাক্টরি বিভিন্নভাবে কারখানার উৎপাদন ধরে রেখে সক্ষমতা দেখানোর সর্বসাধ্য চেষ্টা করছে। যেসব কারখানায় গ্যাসসংকটে ফেব্রিকস উৎপাদন করা যাচ্ছে না, তার মালিকরা অন্য জায়গায় পাঠিয়ে ফেব্রিকস উৎপাদন করছেন। গ্যাসের কারণে কেউ কেউ চীন থেকে ফেব্রিকস নিয়ে আসছেন। এতে নিটওয়্যারশিল্প এখন আমদানিনির্ভর শিল্পে পরিণত হচ্ছে। যে ডলার দেশে থাকার কথা, তা বিদেশে চলে যাচ্ছে। সময়মতো সরবরাহ দিতে না পারলে ক্রেতাদের বিরক্তি ও ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক। তা দেশের গোটা শিল্প খাতকেই ধ্বংসের উপত্যকায় নিয়ে যাচ্ছে।
বিপুল অঙ্কের ব্যাংক ঋণ, উচ্চ সুদের হার, ডলার সংকট, কর্মীদের বেতন-ভাতা, জ্বালানি সংকট, ইউটিলিটি বিলসহ একাধিক খরচের চাপ বিনিয়োগকারীরা কত দিন সইতে পারবে ঠিক বলা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শ্রমিক অসন্তোষ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি তাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়াচ্ছে।
কারখানায় বিক্ষোভ, হামলা-মামলার কারণে ভারী শিল্প, পোশাক ও টেক্সটাইল খাত মারাত্মক সংকটে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে। কারও কারও চলমান ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন। শিল্প খাতে এক বছরের ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। এর প্রভাবে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে ব্যবসার খরচ। টাকার মান কমছেই। মূল্যস্ফীতি আরও বেড়েছে। পরিস্থিতিটা ভোক্তা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সর্বোপরি ধনী-গরিব কারও জন্যই সুখকর নয়। বাস্তবে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে ব্যবসায়ীদের এখনকার বেশি চেষ্টা টিকে থাকার লড়াইয়ে। সেখানে পদে পদে আস্থার ঘাটতি। একদিকে সুদের উচ্চ হার। নয়ছয় সুদ দিয়ে শিল্পবাণিজ্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা টেনে আনতে ছিঁড়ে যায়। এতে কারখানাগুলোই টিকিয়ে রাখা কঠিন। তার পরই না নতুন কারখানা গড়া এবং সেখানে কর্মসংস্থান তৈরি।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেকে ঋণ নিয়ে সেটার অপব্যবহার করেছেন। এ অপকর্মের সঙ্গে অনেক ব্যাংক কর্মকর্তাও জড়িত। অনেক ঋণখেলাপি টাকা নিয়ে বিদেশে চলে গেছেন। লুটপাটের টাকার বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ওই সব টাকা এত দিন খেলাপি করা হয়নি। এখন সেগুলো খেলাপি হচ্ছে। আগে খেলাপি ঋণের প্রকৃত তথ্য আড়াল করে কমিয়ে দেখানো হতো। এখন সব তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এ ছাড়া বেসরকারি কোনো কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা রাজনৈতিক আক্রোশে পড়েছেন। তাদের কারও কারও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কর্মীরা চাকরি হারিয়ে বেকার। কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশের বেশিই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। সরকারি খাতে মাত্র ৫-৭ শতাংশ। অনিবার্যভাবে এখন পুরোনো বেকারের ভিড়ে যোগ হচ্ছে নতুন বেকার।
লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট