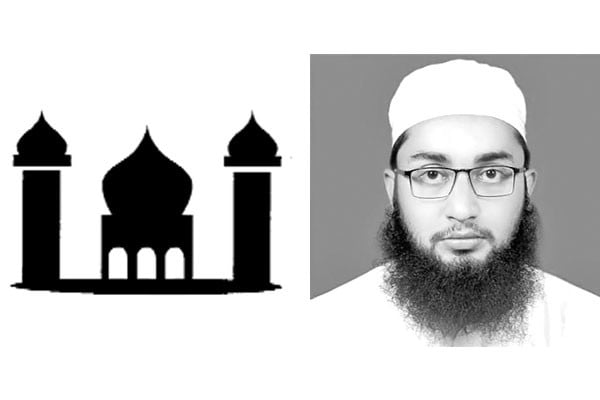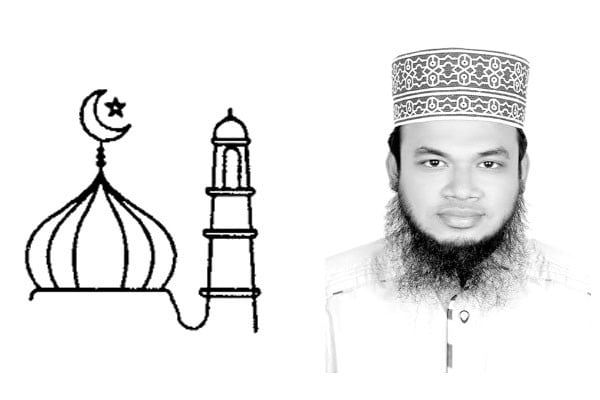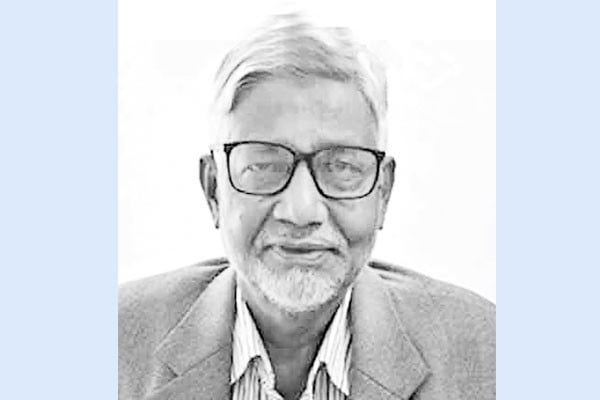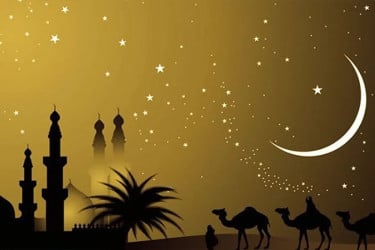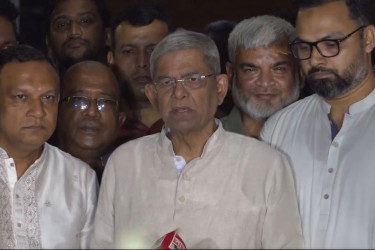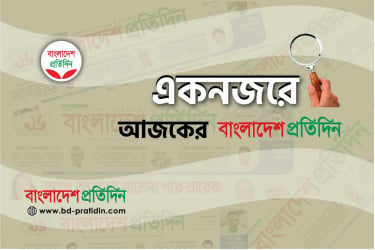বাংলাদেশে এখন ‘রাষ্ট্র সংস্কার’ অন্যতম আলোচিত ও বহুল প্রত্যাশিত বিষয়। দুই হাজার শহীদের আত্মত্যাগ দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছে। এসব উদ্যোগ থেকে একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা করা যায়। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এ ধরনের আশা সরকারসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময় এবং ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক মিল বিদ্যমান, যেখানে উভয় ক্ষেত্রেই দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একত্র হয়েছিল।
পাকিস্তানি শাসন ও আওয়ামী লীগের শাসনের মধ্যে কিছু চরিত্রগত এবং পদ্ধতিগত সাদৃশ্য রয়েছে, যা শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশিদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশ নিতে বাধ্য করেছে। ১৯৭১ সালে, এই অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের ২৩ বছরের শোষণ ও দমন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে। একইভাবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনগণ একটি প্রবল গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত-সমর্থিত ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটায়।
পাকিস্তানি শাসকরা যেমন অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছিল, তেমনি আওয়ামী লীগ সরকার ২৩৪ বিলিয়ন ডলার দুর্নীতি করে সেই অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। উভয় শাসনব্যবস্থাই সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে এবং বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
পাকিস্তানি শাসকরা যেমন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষকে দমন করার চেষ্টা করেছিল, তেমনি আওয়ামী সরকার বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে বিচ্যুত করে একদলীয় ও ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।
উভয় শোষণ পর্বের অবসানই দেশকে পুনর্গঠনের এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে জাতি প্রথম সুযোগটি নষ্ট করেছিল মুজিব সরকারের অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে। যদিও ১৯৭২ সালে প্রশাসন, সংবিধান, শিক্ষা, শিল্প এবং ভূমি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে ডজনেরও বেশি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। দুঃখজনকভাবে, এসব কমিশনের সুপারিশ ও কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই জাতিকে কাঙ্ক্ষিত দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ১৯৭৪ সালে দেশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে নতুনভাবে বিনির্মাণের জন্য যে দক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রয়োজন, তার অভাব তৎকালীন সরকারের কার্যক্রমে প্রকট আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।
মুজিব সরকার ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বছর সময় পেয়েও রাষ্ট্র সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানত চারটি কারণে। চব্বিশের সংস্কার উদ্যোক্তাদের এ থেকে যথেষ্ট শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
 ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র সংস্কারের ব্যর্থতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে দেশ গঠনের জন্য রাজনীতিবিদদের একটি সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অভাব। ষাটের দশকে যখন তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত ছিল, তখন প্রবীণ রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। এর ফলে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ কেমন হবে, তার একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি।
১৯৭২ সালে রাষ্ট্র সংস্কারের ব্যর্থতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে দেশ গঠনের জন্য রাজনীতিবিদদের একটি সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অভাব। ষাটের দশকে যখন তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত ছিল, তখন প্রবীণ রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। এর ফলে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ কেমন হবে, তার একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি।
এই পূর্বপ্রস্তুতির অভাব সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে সংবিধান প্রণয়নের সময়। বাংলাদেশ কোন আদর্শে পরিচালিত হবে, গণতন্ত্র নাকি সমাজতন্ত্র- তা নিয়ে জাতি দ্বিধান্বিত ছিল। পরিশেষে দুই বিপরীত মেরুর দুটি আদর্শকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের অভীষ্ট লক্ষ্য এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে এই অসামঞ্জস্যতা গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। দেশ পরিচালনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে নাকি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে এগোবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা কারও মধ্যেই পাওয়া যায়নি। এর ফলে শেখ মুজিবুর রহমান অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দেশকে একটি অনিশ্চিত যাত্রায় নিয়ে যান। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাকশালের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের সূচনা কোটা আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিবাদ পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। শুরুতেই এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও সরকার পরিচালনাকারীদের মধ্যে দেশ সংস্কারের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তবে ফ্যাসিবাদ পতনের পর বাংলাদেশকে কীভাবে সংস্কারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা অত্যাবশ্যক। গত ছয় মাসে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে সংস্কার কমিশনসমূহ গঠন এবং এতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ অন্যতম। কমিশনের সুপারিশগুলো যদি গণতন্ত্র, বৈষম্যদূরীকরণ, অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তবে জাতি দীর্ঘ মেয়াদে এর সুফল ভোগ করবে বলে আশা করা যায়।
বাহাত্তরের ব্যর্থতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল পাকিস্তানি আমলের আমলাদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসনের অধীনে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম ও অত্যাচারে মদত দেওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের বেতনভুক থেকে শোষণ ও নির্যাতনে অংশ নেওয়া আমলাদেরই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এ ধরনের আমলাতন্ত্র দেশের জন্য একধরনের দ্বি-ধারি তলোয়ারে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ তাৎক্ষণিক কিছু সুবিধা দিলেও, পাকিস্তানি শাসনের ঔপনিবেশিক মনোভাব তাদের মনে বদ্ধমূল থাকায় তারা জনগণের সেবক না হয়ে শোষকে পরিণত হয়। এর প্রভাব আজও সরকারি দপ্তরগুলোতে স্পষ্ট। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও সরকারি কর্মকর্তারা পূর্ণাঙ্গভাবে জনগণের প্রকৃত সেবক হতে পারেননি। বরং ঔপনিবেশিক শাসকরা জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে যে দেয়াল তৈরি করেছিল, তা এখনো টিকে আছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা ফ্যাসিস্ট শাসক বিদায় নিতে বাধ্য হয়। তবে যে প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্র স্বৈরাচারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে, তা এখনো আগের অবস্থানেই রয়েছে। এই নতজানু আমলাতন্ত্র ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের তিনটি নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ করে ফ্যাসিবাদের চাষাবাদ করেছে। এদের ওপর নির্ভর করে নতুন বাংলাদেশের বিনির্মাণ কেবল এক অবাস্তব স্বপ্ন হিসেবেই রয়ে যাবে।
তা ছাড়া যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা এবং দমনপীড়নে মত্ত ছিল, তাদের অপরাধের বিচার না করলে প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মানুষের আস্থা দিন দিন আরও অবনতি হতে থাকবে বলে ধারণা করা যায়।
মুক্তিযুদ্ধের পর যদি নতুন প্রশাসনিক শক্তি গঠন করা হতো, আমলাতন্ত্রের নতুন রূপরেখা তৈরি করা হতো এবং অসাধু কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো দেশ অনেক দূর এগিয়ে যেত পারত। একই কর্তব্য বর্তমান পরিস্থিতির জন্যও প্রযোজ্য। এখনো স্বৈরাচারের প্রেতাত্মা হয়ে থাকা প্রশাসনে যে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা রয়ে গেছে, তাদের হাত থেকে আমলাতন্ত্রকে উদ্ধার করতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে আশঙ্কা থেকে যায়।
মুক্তিযুদ্ধের পরে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার দেশ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর না দিয়ে ভারতনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দেশ বিনির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংবিধান প্রণয়ন। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্থানীয় সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ভারতের সংবিধানের অনুরূপ সংবিধানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।
চব্বিশের অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার বিভিন্নভাবে জনগণকে সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। সুপারিশ প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বিদেশি মডেলের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে কার্যকর আলোচনা করে সুপারিশ তৈরি করা উচিত। যেন সংস্কার প্রক্রিয়া সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে, কমিশনের রিপোর্টের পরিধি বা বিষয়বস্তুর চমকের চেয়ে এর সুপারিশগুলো বাংলাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা, সেটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
অনেকেই মনে করেন, সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট প্রস্তুতিকালীন রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনা না করা একটি ভুল সিদ্ধান্ত। রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা অনেক কঠিন হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সংস্কার সফল করতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প কিছু নেই। রাষ্ট্র সংস্কারে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ‘সর্বজনীন সংস্কার কাউন্সিল’ গঠন করা যেতে পারে। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে মতাদর্শিক বিভাজন দূর করে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
লেখক : পরিচালক, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়